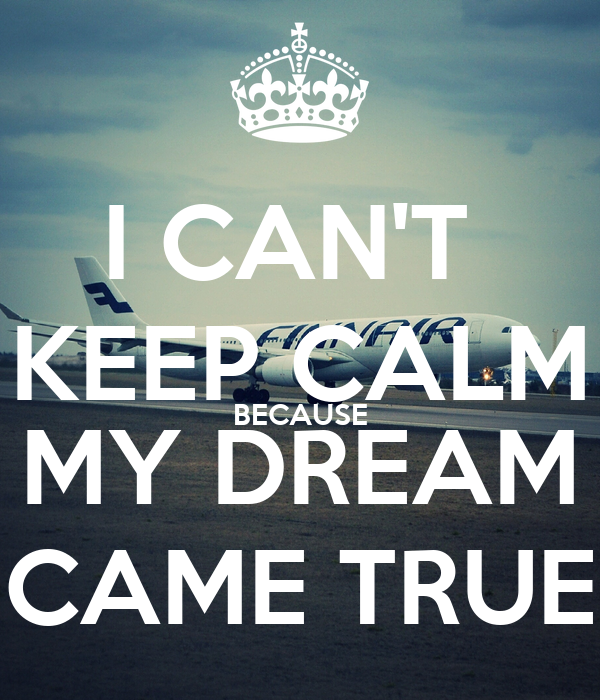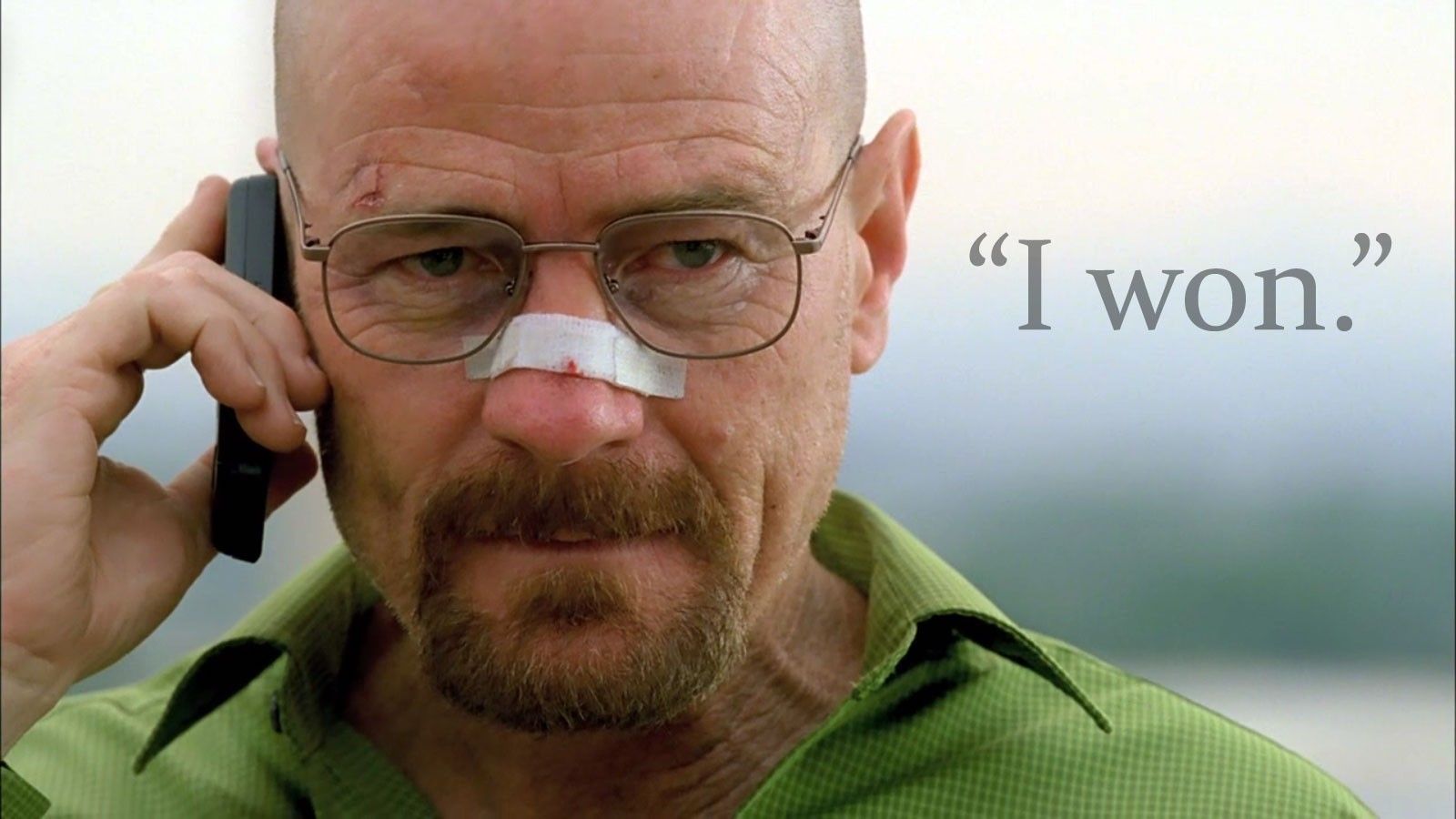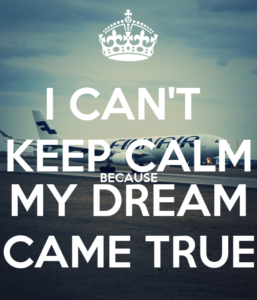পূর্ব কথা
২০১৮ সালের জুনের ২ তারিখ, ভোর ছয়টা। গুলশানের কালাচাঁদপুরের কোনো এক ফ্ল্যাটের মেঝেতে শুয়ে আছি। প্রচণ্ড গরম বলে তোষকে না শুয়ে কাঁথা বিছিয়ে তার উপর শুয়েছি।
প্রতিরাতের মত আজ একটানা ঘুম হয়নি, ভেঙেছে বারবার। গতকাল সন্ধ্যায় সেন্ট লুইস বিশ্ববিদ্যালয়ে ইমেইল পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “অ্যাসিসটেন্টশিপের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানানোর কতো দেরি, পাঞ্জেরি?” আমার মাস্টার্সের ক্লাস শুরু আগস্টের ২৭ তারিখ থেকে, অথচ এখনো ফান্ডের ব্যাপারটা ঝুলে আছে। ফান্ড সম্পর্কে কিছু না জেনে অ্যাডমিশন অফার একসেপ্ট অথবা ডিক্লাইন, কিছুই করা যাচ্ছে না। ভার্সিটি থেকে বলল, ‘চিন্তা নিও না বৎস, আজকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে।’ পিত্তি কেঁপে গেলো। বলে কী? আমি জিজ্ঞেস করার পর তারা বলছে, আজকেই জানিয়ে দেবে? তার মানে আমি ফান্ড পাইনি। যারা ফান্ড পেয়েছে, তাদের নিশ্চয় ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে। যারা পায়নি, তাদের বেলায় গড়িমসি করছে। এই যেমন ঠেলা দেওয়ার পর আমাকে জানানোর ব্যাপারে তাদের মনে পড়লো। তবুও মানুষেরা আমরা ‘কী আশায় বাঁধি খেলাঘর!’ ইমেইল আসার আগ পর্যন্ত আমি আশা নিয়ে বসে রইলাম।
প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ঘুম ভেঙে যায়। চোখ ডলতে ডলতে মোবাইলে ইমেইলের নোটিফিকেশন চেক করি। ফক্কা। সারারাত এভাবে কাটার পর পাঁচটার দিকে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। কিন্তু সাতটার দিকে আবার জাগনা। তড়িঘড়ি মোবাইল হাতে নিলাম। এসেছে কোনো মেইল? হ্যাঁ! ঐ তো স্ক্রিনে নোটিফিকেশন দেখাচ্ছে। নার্ভাস হাতে মেইল খুললাম। ‘Hello Nirjhar, Congratulations!!’ পর্যন্ত দেখে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো। এরপর আর পড়তে পারছি না। অভিনন্দন দেয় কেন? ফান্ড পেয়েছি নাকি? ধীরে ধীরে তাকালাম পরের বাক্যের দিকে। ‘You have been awarded a Graduate Assistantship in the Department of Nutrition and Dietetics at Saint Louis University. I look forward to hearing from you soon.’ চোখ ডলে দুইবার পড়লাম। আসলেই পেয়েছি? জীবনে প্রথমবারের মত আমি ফান্ড পেয়েছি? ইমেইলের সাথে এমএস ওয়ার্ড ফাইলে টাইপ করা একটা কন্ট্রাক্ট পাঠানো হয়েছে। ওখানে ফান্ড সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা। প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমার চোখ ভর্তি করে জল এলো। এই দিনের জন্য আমি চারটা বছর অপেক্ষা করেছি। অনেকে দুই বছরে হাল ছেড়ে দেন। কিন্তু আমি চার বছর ধরে লেগে রয়েছি আমেরিকায় পড়তে যাওয়ার পেছনে। অন্য কোনো দেশ নয়, অন্য কোনো মহাদেশ নয়, আমি যাবো উত্তর আমেরিকা মহাদেশের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নামক দেশে। এটাই পড়াশোনার জন্য আমার স্বপ্নের দেশ।
পাশে হাজবেন্ড গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। তেনাকে উত্তেজনার ঠ্যালায় ঝাঁকি মেরে উঠালাম। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বেচারা ‘কী হইছে? কী হইছে?’ বলে লাফিয়ে উঠল। আমার এলোকেশ আর ঘুমহীন চেহারা দেখতে নিশ্চয় মন্ত্রমুগ্ধকর ছিল না! তার উপর ঘুম ঘুম চোখে আমার মুখের হাসিকে ‘রহস্যময়’ বা ‘ভৌতিক’ ধরে নিয়ে সে আরও ঘাবড়ে গেলো। বললাম, ‘অ্যাসিসটেন্টশিপ পেয়েছি! ফল ২০১৮-এর জন্য।’
আমার একত্রিশ বছরের জীবনে পড়ালেখা সংক্রান্ত সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে আমি একেই ধরি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিজৌরি স্টেটের সেন্ট লুইস শহরে অবস্থিত ‘সেন্ট লুইস বিশ্ববিদ্যালয়ের’ “Doisy College of Health Sciences”-এর অন্তর্গত Department of Nutrition and Dietetics-এর Medical Dietetics নামক মাস্টার অফ সায়েন্স প্রোগ্রামে ফান্ডসহ ভর্তির সুযোগ পাওয়া। ফান্ড ছাড়া অ্যাডমিশন বেশ কয়েকবারই পেয়েছি, কিন্তু ফান্ডসহ অ্যাডমিশন অর্জনের জন্য আমাকে যেভাবে কষ্ট করতে হয়েছে, সেভাবে মনে হয় না অনার্স মাস্টার্সের আট বছর (সেশন জটের ঘোরপ্যাঁচে পড়ে) কষ্ট করেছি! তাই ঠিক করেছি একটা লেখা লিখবো সকল অভিজ্ঞতা নিয়ে। লেখার মূল কারণ, কেউ যেন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে না দেয়। এখানে আমি গল্প করবো আমার অ্যাডমিশনের পেছনের কাহিনি নিয়ে। যে পরিমাণ ধৈর্য, অধ্যবসায়, হতাশা, বিষণ্ণতা আর কষ্ট পার করে আজ আমি আমেরিকায় মাস্টার্স করতে এসেছি, সে গল্প অন্যদের উৎসাহিত করবে বলে আমার ধারণা। এই গল্পের দুটো পর্ব। প্রথম পর্বে আছে কীভাবে উচ্চশিক্ষার পেছনে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম সেই গল্প, দ্বিতীয় পর্বে ছোটার মধুরেণ সমাপয়েৎ।
প্রথম পর্ব
ছোটবেলা থেকেই মা আমার মাথায় পিএইচডির স্বপ্ন বুনে দিয়েছিলেন। মা অত্যন্ত পড়াশোনাপ্রিয় মানুষ। সারাজীবন ধরে ফার্স্ট ক্লাস রেজাল্ট করে এসেছেন। টানা অনেক বছর ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (প্রাক্তন পিজি হাসপাতাল) নার্সিং অনুষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। এমন মায়ের সন্তান হয়ে জেনেটিক্যালি আমার লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু না, আমি ছিলাম ত্যাঁদড়। ক্লাস সিক্সে উঠার আগ পর্যন্ত জানতামই না প্রথম হতে কেমন লাগে। তবে অষ্টম শ্রেণির সরকারি বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে প্রথম স্থান অধিকার করে সবার মনে ভাল ছাত্রের আসন করে নিলাম। এরপর এসএসসিতে জিপিএ ৪.৮৮ (২০০৩ সালের কথা। তখন ফোর্থ সাবজেক্টের জিপিএ যোগ হত না। হলে আমি জিপিএ ৫ পেতাম। হাহা!) পেয়ে স্কুলের মধ্যে সেরা রেজাল্ট করলাম। চলে এলাম ঢাকার হলি ক্রস কলেজে। শুরু হল আমার উড়নচণ্ডী জীবন। এইচএসসি পরীক্ষায় ডাব্বা মারলাম (জিপিএ ৩.৯০)। আমার অধঃপতনে সবাই অবাক হল কিন্তু আমি খুব খুশি হলাম ফলাফল দেখে। আমার যেখানে পাশ করারই কথা ছিল না রসায়নে, সেখানে ৩.৯ মেলা কিছু। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষাগুলোতে ডাব্বা মারলাম। ধারাবাহিক ডাব্বা মারা শেষ হল যখন আজিমপুরে অবস্থিত গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলাম। পছন্দের ভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারিনি বলে অনার্সে সিরিয়াসলি পড়াশোনা করিনি। রেজাল্ট এলো সেকেন্ড ক্লাস। এই ফলাফল দিয়ে কোথায় চাকরি পাবো? এর মধ্যে বেশ কিছু ক্লাসমেট ভাল রেজাল্ট করে ‘পুষ্টিবিদ’ হিসেবে ঢুকে গেলো নামী দামী হাসপাতালে। তাদের দেখে আমার মাথায়ও চাকরির চিন্তা ঢুকলো। মাস্টার্সের ক্লাস শুরু হতে তখনও ছয়-সাত মাস বাকি। সে সময় আমার খালা একটা চাকরির প্রস্তাব নিয়ে এলেন। বাংলাটেক্স নামক ইতালীয় বায়িং হাউজ গাজীপুরে ওয়ারহাউজ খুলেছে। সেখানে কম্পিউটার অপারেটরের চাকরি। তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিলাম ঢুকে যাওয়ার। এই পর্যায়ে জীবনটা সরলরেখা থেকে বক্ররেখায় যাত্রা শুরু করলো।
চাকরিতে ঢোকার তিন মাসের মাথায় আমার পদোন্নতি হলো। কম্পিউটার অপারেটর থেকে হয়ে গেলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার অফ ওয়ারহাউজ। বেতনও দ্বিগুণ হলো। আটকা পড়ে গেলাম অর্থের লোভে। মনে হলো, মাস্টার্স করে কী লাভ? পুষ্টিবিজ্ঞানের চাকরির শুরুতেও তো একই বেতন। এর চেয়ে এখানেই থাকি, বছর শেষে আরেকটা ইনক্রিমেন্টের সম্ভাবনা আছে। ক্লাস করি বা না করি, চাকরির মাঝখানে ঠিকই ভর্তি হয়েছিলাম মাস্টার্সে। ভেবেছিলাম চাকরি করবো আর মাঝে মাঝে ক্লাস করে হাজিরা ঠিক রাখবো। কিন্তু চাকরি করতে গিয়ে ক্লাস, পড়াশোনা কিছুই হচ্ছিলো না। সিদ্ধান্ত নিলাম মাস্টার্স ড্রপ দেওয়ার। বাঁধ সাধলেন বাবা-মা। বললেন, “মাস্টার্স ড্রপ দিয়ে চাকরি চালানোর দরকার নাই। একটা ডিগ্রি অর্জন করার পথে অর্ধেক গিয়ে অর্ধেক বাকী রাখার মানে হয় না”। কিন্তু মনকে কিছুতেই মানাতে পারলাম না। মাথায় ঢুকে গেছে, আমাকে পুষ্টিবিদ নয়, টেক্সটাইল মার্চেন্ডাইজার হতে হবে। আমার অনেক আত্মীয় স্বজনই এই পেশায় আছেন। তাঁদের দেখে আমি উৎসাহিত হয়ে উঠি। বাবা-মাকেও বুঝাই। বাবা-মা হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, “আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে বিজিএমইএ থেকে প্রফেশনাল কোর্স কর মার্চেন্ডাইজিংয়ের উপর”। আমি রাজী হলাম। অ্যাডমিশন টেস্ট দিলাম, টিকেও গেলাম। কিন্তু ঝামেলায় পড়লাম শিফট নিয়ে। দুই শিফটে ক্লাস হয়। কিন্তু কোনো শিফটই আমার জন্য সুবিধার না। গাজীপুর থেকে অফিস শেষ করে আসতে আসতে ক্লাস খতম হয়ে যাবে। ফলে যেই কে সেই। এখানেও বাদ দিতে হলো কোর্সের আশা।
এবার বাবা-মা ক্ষেপে গেলেন। রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বললেন, “আমাদের কোনো কথাই তুমি শুনছো না। মাস্টার্স করতে বললাম, সেটা করলে না। তোমার ইচ্ছেমত মার্চেন্ডাইজিং নিয়ে পড়তে বললাম, সেটাও পড়লে না। কী সমস্যা তোমার?” আমিও ভাবতে শুরু করলাম, কী সমস্যা আমার। এরপর শান্ত হয়ে পিতামাতা বললেন, “চাকরি অনেক আসবে যাবে। কিন্তু সুযোগ নষ্ট হয়ে গেলে মাস্টার্স আর করা হবে না জীবনে। এখনো তুমি লেখাপড়া থেকে খুব একটা বিচ্যুত হওনি। কিন্তু দুই তিন বছরের গ্যাপ পড়লে এই কলেজ থেকে মাস্টার্স করার সুযোগ থাকবে না। যেহেতু ভর্তি হয়েছিলেই, পরীক্ষা দেওয়াটা ফরজ”। চিন্তা করে দেখলাম উনারা ঠিকই বলছেন। নিজের সাথে বেশ কয়েক রাত যুদ্ধ করে হুট করেই সিদ্ধান্ত নিলাম চাকরি ছেড়ে দেবো। যা থাকে কপালে, মাস্টার্স শেষ করবো। পরীক্ষার বাকি আছে পাঁচ মাস। সবাই বারো মাস ধরে প্রস্তুতি নিবে, আর আমাকে পাঁচ মাসের মধ্যে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় বসতে হবে। ধুমসে পড়া দিলাম। নিয়মিত ক্লাস করা শুরু করলাম, এর ওর কাছ থেকে নোট যোগাড় করতে লাগলাম। আদা জল খেয়ে লাগা আর কি। কষ্টের ফল হিসেবে কেষ্টও মিললো। মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাস এলো। পরীক্ষা শেষের সাথে সাথে একজন গবেষকের অধীনে দুই মাস কাজ করার সুযোগ পেলাম। ঐ কাজ করতে করতেই সুযোগ এলো VLCC নামক একটা ফিটনেস সেন্টারে পুষ্টিবিদ হিসেবে চাকরি করার। যোগ দিলাম। কিন্তু একমাসের মাথায়ই পুরনো বায়িং হাউজ থেকে প্রস্তাব এলো নতুন পোস্টে চাকরি করার। বেতন খুব ভালো বলে VLCC-তে ইস্তফা দিয়ে চলে এলাম এখানে। দিন শেষে টাকাটাই মুখ্য ছিল আমার মধ্যবিত্ত সত্ত্বার কাছে।
এতো উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে পিএইচডি করার স্বপ্নটা প্রায় মুছেই গিয়েছিলো। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, বায়িং হাউজে ঢুকে স্বপ্নটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। এবার একদম ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পদ্মা নদীর মত। বারবার মনে হতে লাগলো, আমি কেন আমার স্বপ্নের পিছু ছুটছি না? কেন টাকা টাকা করে নিজেকে বন্দী করে ফেলছি সীমিত পরিসরে? আমার জন্ম শুধু পুষ্টিবিদ হিসেবে হাসপাতালে বা কোয়ালিটি ম্যানেজার হিসেবে বায়িং হাউজে চাকরি করার জন্য নয়। আমার জন্ম আরও বড় কিছুর জন্য। গবেষণার জন্য, মানুষের উপকারে লাগার জন্য। সেই সাথে পুষ্টিবিজ্ঞানের উপর নতুন করে টান অনুভব করলাম। অনার্স মাস্টার্সে পুষ্টিবিজ্ঞানের উপর যে ভালোবাসাটুকু থাকলে ভালো ফলাফল করতে পারতাম, সে প্যাশন চাগিয়ে উঠলো চাকরিতে ঢোকার পর। আগেই বলেছি ছোটবেলা থেকে মা পিএইচডি ব্যাপারটা মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা যে আসলে কী, কীভাবে করে, কেন করে – উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত আমি কিছুই বুঝতাম না। শুধু বুঝতাম আমাকে ডিগ্রিটা নিতে হবে। পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের আমি গ্রহান্তরের মানুষ ভাবতাম। অনার্সের আগ পর্যন্ত কোনো পিএইচডিধারীকে সামনাসামনি দেখার সুযোগ হয়নি। তাই তাদের বিষয়ে আমি অনেক কিছু কল্পনা করে নিয়েছিলাম। যেমন, অনেক বেশি বয়সে মানুষ এই ডিগ্রি লাভ করে, এই ডিগ্রিধারীরা অহংকারী, ধরাছোঁয়ার বাইরে, সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন না ইত্যাদি। অনার্সে উঠে প্রথম এক দম্পতিকে দেখেছিলাম যারা দুইজনই পিএইচডি করা। তখন থেকে মাথায় ঘুরত, আমিও পিএইচডি শেষ করে একজন পিএইচডিওয়ালাকে বিয়ে করবো। মোট কথা, এই ডিগ্রিটার প্রতি ছিলো আমার আজন্ম সাধ।
তাই চাকরির পাশাপাশি জোরেশোরে লাগলাম বিদেশে পিএইচডি করার পেছনে। এটা ২০১৩ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির কথা। তখন সবেমাত্র ফেসবুকের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত গ্রুপ “হায়ার স্টাডি অ্যাব্রোড”-এর সাথে পরিচয় ঘটেছে। প্রতিদিন এই গ্রুপের পোস্ট, পোস্টের মন্তব্য আর ডকুমেন্টগুলো পড়ি। এভাবে কিছুটা ধারণা পেলাম বাইরে উচ্চশিক্ষার বিষয়ে। কয়েকমাস গবেষণার পর বুঝলাম আমার সামনে দুটো অপশন খোলা। এক, ইউরোপ থেকে পুষ্টিবিজ্ঞানের উপর মাস্টার্স করে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়া থেকে পিএইচডি করা (কারণ ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পুষ্টিবিজ্ঞানের উপর পিএইচডি কোর্স এভেইলেবল নয়। এক ভাই পরামর্শ দিয়েছিলেন Erusmus Mundus স্কলারশিপ নিয়ে ইউরোপে মাস্টার্স করতে। তাহলে আমার প্রোফাইল ভারী হবে); দুই, আমেরিকায় সরাসরি পিএইচডিতে ভর্তি হওয়া। কিন্তু আমার গবেষণা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা খুব কম (অনার্সের থিসিস ছাড়া) বলে ধরে নিয়েছিলাম আমেরিকায় সুযোগ পাওয়া সম্ভব না। মে-জুনের দিকে ফেসবুকের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত আরেকটা গ্রুপ “নেক্সটপ ইউএসএ”-এর প্রতিষ্ঠাতা ফরহাদ হোসেন মাসুম আমাকে নিশ্চিত করলো, গবেষণার অভিজ্ঞতা ছাড়াও আমেরিকায় পিএইচডি করতে যাওয়া সম্ভব। প্রয়োজন শুধু সঠিক উপায়ে আগানো। মানে আপনার যদি একাডেমিক প্রোফাইল দুর্বল হয়, তাহলে GRE, TOEFL/IELTS ইত্যাদি পরীক্ষায় ভালো স্কোর তুলে, ভালো রেকোমেন্ডেশন যোগাড় করে সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠা যায়। শুনে আমি দ্বিগুণ উৎসাহে আমেরিকা বিষয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম। ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখলাম, আমেরিকার যে পরিমাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পুষ্টিবিজ্ঞান অনুষদ আছে, অন্য দেশে সে সংখ্যক নেই। তার মানে আমেরিকায় গবেষণার স্কোপ অনেক বেশি, ফান্ড বেশি।
উৎসাহ তুঙ্গে উঠলো। সমানে বিভিন্ন গ্রুপের ডকুমেন্ট পড়ি, ভার্সিটি খোঁজাখুঁজি করি, রিসার্চ ইন্টারেস্ট মিলিয়ে প্রফেসর বের করি, GRE- IELTS পরীক্ষার প্রস্তুতি নিই। কিন্তু GRE বই ঘেঁটে বুঝলাম, প্রস্তুতি পর্ব শুরু করতে আমার বেশ দেরি হয়ে গেছে। সবকিছু এমন কঠিন যে, পড়ে শেষ করতে অন্তত ছয় মাস লাগবে। আর ছয় মাস পর পরীক্ষা দিলে ফল ২০১৫ ধরা যাবে না। ঝোঁকের বশে সিদ্ধান্ত নিলাম ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে যা আছে কপালে ভেবে GRE দিয়ে দেবো। ভালো স্কোর আসলে কয়েক জায়গায় এপ্লাই করব, নাহলে আবার পরীক্ষা দেবো। এর মাঝে ঘটে গেলো এফেয়ার সংক্রান্ত বিপদ। মানসিকভাবে ভেঙে পড়লাম। পড়াশোনা তো লাটে উঠলোই, আমেরিকায় যাওয়ার স্বপ্ন থেকেও সরে আসতে লাগলাম। যখন জানুয়ারি মাস এলো, পরীক্ষায় না বসার সিদ্ধান্ত নিলাম। একদমই কিছু পড়িনি, কী পরীক্ষা দেবো? ঠিকমতো পরীক্ষার নিয়ম কানুনও জানি না। কিন্তু বাবা-মায়ের চাপাচাপিতে পরীক্ষা দিলাম, স্কোর এলো ২৮৭। এই স্কোর নিয়ে কী করবো? তারপরও চারটা ভার্সিটিতে ফ্রি স্কোর পাঠিয়ে দিলাম। বলা বাহুল্য, কোনো ভার্সিটিতেই শেষ পর্যন্ত এপ্লাই করিনি। বিচ্ছেদের ঠ্যালায় নাওয়া খাওয়া ভুলে সারাদিন হতাশ আর বিষণ্ণ হয়ে পড়ে থাকি। অফিস ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, পালিয়ে যাই নতুন কোনো জায়গায় যেখানে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবো। হঠাৎ মাথায় এলো, যদি আমেরিকায় পিএইচডি করার সুযোগ পেয়ে যাই, তাহলেই তো নতুন জীবন শুরু করতে পারবো! ফলে আবারও স্বপ্নটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। ২০১৪ সালের মার্চ-এপ্রিল থেকে পুরোদমে GRE আর IELTS পড়া শুরু করলাম। ঠিক করলাম, যে করেই হোক ২০১৫ সালের ফল সেশন আমাকে ধরতেই হবে। এজন্য পরীক্ষাগুলো দিয়ে দিতে হবে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরের ভেতর।
২০১৫ সালের ফল সেশন ধরার চেষ্টা
অফিসের উদ্দেশ্যে আমি সকাল সাড়ে সাতটায় বের হতাম, ফিরতাম রাত সাড়ে আটটায়। অসহনীয় যানজটের কারণে আমাকে তিন ঘণ্টা রাস্তায় কাটাতে হতো, আর দশ ঘণ্টা ছিলো অফিস টাইম। বুঝুন! রাতে বাসায় ফিরে কি আর পড়তে ইচ্ছে করে? জ্যাম্প্যাকড মাথা নিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে পড়তাম। স্কুল জীবনে পড়া অনেক গাণিতিক সূত্র নতুন করে পড়তে হচ্ছিলো কারণ সেগুলো ভুলে গেছি। সাথে নতুন গাণিতিক কৌশল, সূত্র, আজদেহা ইংরেজি তো আছেই। ছোটো দুই ভাই, তাদের বন্ধু, আমার বন্ধু সবাইকে জ্বালিয়েছি GRE পড়তে গিয়ে। ওরা না থাকলে অনেক অংকই আমার না-বুঝা থেকে যেতো। মাঝে মাঝে মনে হতো, সেপ্টেম্বরে বুঝি পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব না। আরও অন্তত এক বছর লাগবে আমার প্রস্তুতি নিতে। কিন্তু তারপরই মনে হতো, এক বছর পিছিয়ে যাওয়া কোনো কাজের কথা না। যত কষ্টই হোক, পরীক্ষাটা ২০১৪ সালেই দিতে হবে। নতুন উপায় হিসেবে অফিসে বসে পড়া শুরু করলাম। দুপুরের খাওয়ার সময় তো পড়তামই, কাজের ফাঁকেও অনেক সময় অংক কষেছি। যেহেতু IELTS পরীক্ষার ফলাফল দিতে দুই সপ্তাহ সময় লাগে, তাই এই পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন আগে করলাম। যখন পরীক্ষার মাত্র এগারোদিন বাকি, তখনো পর্যন্ত IELTS-এর বইগুলো আমার ধরা হয়নি। আগস্টের ১৬ তারিখ ছিল পরীক্ষা। ছয় তারিখ থেকে শুরু করলাম ক্যামব্রিজ IELTS ১-৯ বইয়ের ম্যারাথন অনুশীলন। তবে পড়ার আগে অন্তর্জাল থেকে IELTS-এর বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে গবেষণা করে নিলাম। এইসব কৌশলই আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। আপনি যদি বাসায় বসে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে পড়াশোনা করেন, তাহলে IELTS বা GRE কোনোটার জন্যেই কোচিং সেন্টারে ছুটতে হবে না। প্রয়োজন শুধু আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাসটুকু আমার গড়ে উঠেছিলো।
যখন সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে GRE দিলাম, তখন GRE বিষয়ে আমার প্রস্তুতি আধাখ্যাচড়া মার্কা। ঐ অবস্থায়ই পরীক্ষা শেষ করলাম, স্কোর এলো ৩০২। যদিও আগের ২৮৭-এর তুলনায় ভালো, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ৩০৫ পাবো। দশদিনের ঝটিকা প্রস্তুতির তুলনায় আশা করেছিলাম IELTS-এ ৭ পাবো। কিন্তু হতাশ করে দিয়ে স্কোর এলো ৬.৫ । তাই GRE আর IELTS পরীক্ষা দুটোর হতাশাব্যঞ্জক ফলাফল নিয়েই প্রফেসরদের নক করতে শুরু করলাম। উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগুলোর প্রস্তুতি নেওয়া, পরীক্ষা দেওয়া কিংবা পরীক্ষা পরবর্তী কাজগুলো করা মিলিয়ে পুরো প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী। আপনি একটা স্টেপ শেষ করবেন, দেখবেন সামনে পড়ে আছে আরও কঠিন একটা ধাপ। সেটা শেষ করে দেখবেন, আরেকটা জবরজং ধাপ অপেক্ষমান। মূল বিষয় হলো, আপনি কতোটা ধৈর্য নিয়ে ধাপগুলো পার হতে পারছেন। একেক সময় আমার ধৈর্য বটিকার মেয়াদ শেষ হয়ে যেতো। প্রচণ্ড বিরক্ত লাগতো জগত সংসারের উপর। যখন একজনও প্রফেসরকে নক করে পজিটিভ রিপ্লাই পাবেন না, তখন বুঝবেন how life fucks us।
২০১৪ সালে প্রথম দফায় মোট পাঁচটা ভার্সিটিতে আবেদন করেছিলাম। দুঃখের ব্যাপার হলো, আমি সঠিক উপায়ে খোঁজাখুঁজি করিনি। ফলে অনেক ভার্সিটিই আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে রয়ে গিয়েছিলো, আর ইমেইল করার জন্য খুঁজে পেয়েছিলাম খুব কম সংখ্যক প্রফেসরকে। এর মধ্যে ঘটেছিলো আরেক বিপদ। মাত্র পাঁচ-ছয়জন প্রফেসরকে ইমেইল করার পরই একজন খুব আগ্রহ দেখিয়ে উত্তর দিলেন। আমি তো খুশিতে আত্মহারা! অনেকে নাকি দেড়শো দুইশো ইমেইল দেওয়ার পরও ইতিবাচক প্রত্যুত্তর পান না, অথচ আমার ইমেইলের সংখ্যা দশের কোটাও পেরোয়নি, এখনই পজিটিভ ইমেইল চলে এসেছে। ইয়াহু! ঐ প্রফেসরের সাথে আমার বিশবারের মত ইমেইল আদান প্রদান হলো। দ্রুত এপ্লাই করে ফেললাম। পুরোপুরি নিশ্চিত যে, এখানেই হবে। ফলে অন্য প্রফেসর খোঁজার কাজে ঢিলেমি চলে এলো। এরপর মাত্র বিশ/পঁচিশজনকে নক করলাম। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কেউই আমাকে পজিটিভ কিছু বলেননি, শুধু জেনেরিক রিপ্লাই দিয়েছেন। তাই বিরক্ত হয়ে ইমেইলিং ক্রয়ায় ইস্তফা দিলাম। উনাদের জেনেরিক রিপ্লাইয়ের উপর ভিত্তি করেই আমার বদখৎ প্রোফাইল অনুযায়ী আরও চারটাতে আবেদন করলাম (নিরাপদ থাকার জন্য)। কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আত্মবিশ্বাস ভালো হলেও অতি-আত্মবিশ্বাস ধ্বংসের কারণ। কেন, সে ব্যাপারে একটু পরেই আসছি। বলে রাখা ভালো, আপনি রেকোমেন্ডেশন লেটার সাবমিট করা ছাড়াই অনলাইন এপ্লিকেশন সাবমিট করে দিতে পারেন। লেটারগুলো পরে (কিন্তু ডেডলাইনের ভিতরে) সাবমিট করলেও চলে। আমার ইচ্ছা ছিলো, পুরো প্যাকেজ একসাথে সাবমিট করা। কিন্তু প্রফেসরদের গড়িমসির কারণে এপ্লিকেশনের সাথে লেটারগুলো সাবমিট করতে পারিনি।
যে তিনজন টিচারকে রেকোমেন্ডার হিসেবে ঠিক করেছিলাম, তাদের মধ্যে একজন চাওয়ামাত্রই দিয়ে দিলেন, আরেকজন অনলাইনে দিতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিলেন (কারণ তিনি এই পদ্ধতির সাথে পরিচিত নন। তিনি পেপার লেটার দিতে আগ্রহী), এবং শেষজন দেবেন দেবেন বলে আমাকে টানা দুইমাস ঘুরালেন। যদি প্রথমেই তিনি বলে দিতেন “পারবো না”, আমি আরেকজনকে ঠিক করতাম। কিন্তু তিনি দিচ্ছি দিবো করে করে দুইমাস কাটিয়ে তারপর দিলেন। যা হোক, ডেডলাইন দরজায় কড়া নাড়ছে কিন্তু দ্বিতীয় প্রফেসরের লেটারটা আমার যোগাড় করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত ডেডলাইনের দিন দ্বিতীয় টিচারের বাসায় গিয়ে অনলাইনে কীভাবে রেকোমেন্ডেশন দিতে হয়, সেটা নিজে শিখলাম, উনাকেও শিখালাম। উনি আমাকে বলছিলেন, “সবই খোদার হাতে। আজ যদি সাবমিট করতে না পারি, তাহলে খোদা চাচ্ছেন না তুমি চান্স পাও।” ঐ মুহূর্তে আমি হতভম্ব হওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। কথা শুনে শুধু কান্নাই পেয়েছিলো। এখন বুঝি, ভুল আমারই হয়েছিলো। ব্যাকআপ রাখা দরকার ছিলো। একজন প্রফেসর ঘুরাতে থাকলে যে আরেকজনকে অনুরোধ করব, এই চিন্তাটাই মাথায় আসেনি। যখন অ্যাডমিশন ডিসিশন এলো, আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, ঐ নিশ্চিত হওয়া প্রফেসরের ভার্সিটি থেকে আমাকে এক্সেপ্টেন্স লেটার পাঠানোর বদলে নম্র ভদ্র একটা রিজেকশন লেটার পাঠানো হয়েছে। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। দিনটা ছিলো ২০১৫ সালের ১৭ জানুয়ারি, সকালবেলা। আমি বাসে করে অফিসে আসছিলাম। মোবাইলে ইমেইল চেক করতে গিয়ে এই রিপ্লাই দেখলাম। নির্ঘাত বাসে ছিলাম, নইলে কেঁদেই ফেলতাম। যেটার বিষয়ে আমি ১০০% নিশ্চিত ছিলাম, সেখান থেকেই রিজেকশন এলো। বাকি যে চারটায় আবেদন করেছি, সেগুলো থেকে কী রিপ্লাই আসতে পারে অনুমান করে শীতর মধ্যেও গরম লাগতে থাকলো। পায়ের তলা থেকে দ্বিতীয়বার মাটি সরে যাওয়ার অনুভূতি পেলাম। প্রথমবার পেয়েছিলাম বিচ্ছেদের সময়।
যা হোক, দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী কাটতে লাগলো বাকি চারটা সিদ্ধান্ত আসার অপেক্ষায়। এর মধ্যে এক ছোটবোন (সেও পুষ্টিবিজ্ঞানে স্নাতক এবং আমেরিকায় পিএইচডির জন্য এপ্লাই করেছে) তাগাদা দিতে থাকলো আরেকটা মিডল র্যাঙ্কের ভার্সিটিতে এপ্লাই করার জন্য। তার এক পরিচিত ব্যক্তি ওখানে গিয়েছেন নিউট্রিশনের উপর পড়তে। আমি তখন নার্ভাস আর ভীত। একদম শেষ মুহূর্তে এপ্লাই করলাম ঐ ভার্সিটিতে (SDSU)। ওখানকার এক্সেপ্টেন্স রেট অত্যন্ত বেশি। আশা জন্মালো, হয়তো হয়ে যাবে। কিন্তু না, এটাসহ আরও চারটা ভার্সিটি থেকে রিজেকশন এলো। বাকি রইলো ইউনিভার্সিটি অফ ক্যানসাস মেডিক্যাল সেন্টার (KUMC)। এটার আশা একদমই ছেড়ে দিলাম। সাধারণত জেনারেল ডেডলাইন পার হওয়ার এক/দুই মাসের মধ্যে ভর্তির ফলাফল জানানো হয়। কিন্তু দুই মাস পার হয়ে গেলেও KUMC থেকে কোনো সিদ্ধান্ত এলো না। ব্যাপার কী? রিজেকশন হলেও তো সেটা আমাকে জানাবে, নাকি? শেষে নিজেই উদ্যোগী হয়ে ডিপার্টমেন্টে নক করে জানতে চাইলাম, কবে নাগাদ সিদ্ধান্ত জানতে পারবো। বেশ একটা চমক খেলাম। ওরা বললো, “তোমাকে আমরা অ্যাডমিশন দিতে পারি, কিন্তু এই মুহূর্তে ফ্যাকাল্টিদের হাতে পিএইচডি স্টুডেন্টকে সাপোর্ট করার মত ফান্ড নেই। যদি তোমার নিজের ফান্ড থাকে, তুমি ফল ২০১৫-এ আসতে পারো।” প্রচণ্ড খুশি হলাম। অন্ততপক্ষে একটা ভার্সিটি থেকে অ্যাডমিশন তো পেয়েছি! কিন্তু এরপরই ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেলাম। নিজের ফান্ড যোগাড় করা দুঃসাধ্য। অনুরোধ করলাম আমার ভর্তি ফল-২০১৬ পর্যন্ত ডিফার করতে। যদি তখন কেউ ফান্ড পান এবং আমাকে নিতে চান, আমার যেতে কোনো সমস্যা নেই। এখন কথা হলো, শুধু KUMC-এর উপর নির্ভর করে ফল ২০১৬-এর আশায় বসে থাকাটা বোকামি হবে। এমনিতে ফল ২০১৫-এ আমি যথেষ্ট পরিমাণ বোকামি করেছি। আবার ঝুঁকি নিয়ে ফের KUMC-এর ফ্যাকাল্টিদের কাছ থেকে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত শুনে ফল ২০১৬ পার করার মানে হয় না। তাই ঠিক করলাম ফল ২০১৬ ধরার জন্য সংগ্রামে নামবো।
২০১৬ সালের ফল সেশন ধরার চেষ্টা
সময় তখন ২০১৫ সালের এপ্রিল মাস। মাথায় জিদ চেপে গেছে আমেরিকা যাওয়ার। যখন দেখি আমার চেয়ে কম সিজিপিএ/GRE/IELTS/TOEFL/শূন্য গবেষণা অভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষের ফান্ডসহ অ্যাডমিশন হয়ে যাচ্ছে, তখন একইসাথে হতাশ আর উদ্যমী লাগে নিজেকে। এরমধ্যে ছোটবোনের পিএইচডি অ্যাডমিশন হয়ে গেলো হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে। ও আমার চেয়ে চার বছরের জুনিয়র। কিন্তু ওর সিজিপিএ-TOEFL-গবেষণা অভিজ্ঞতা অনেক ভালো বলে স্নাতক ডিগ্রি দিয়েই ২০১৫-এর ফলে ওর হয়ে গেছে। কিন্তু আমি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েও সুবিধা করতে পারছি না। অবশ্য ছোটবোনর মত হাই প্রোফাইল স্টুডেন্টেরও ফুল ফান্ড যোগাড় করতে কালো ঘাম ছুটে গেছে। সেই জায়গায় আমার মত মিডিয়াম প্রোফাইলধারীর লাল সুতা বের হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? তার উপর ছোটবোন ওর অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারলো, মৌলিক পুষ্টিবিজ্ঞানে ফান্ড কম। পাবলিক হেলথে অনেক ফান্ড, কিন্তু সেখানে বেশিরভাগই মাস্টার্স ডিগ্রি (MPH) নিতে যায়, পিএইচডি স্টুডেন্ট বেশ বিরল। আর “ফুড সায়েন্স” শাখাটায় আমাদের দুজনের কোনো আগ্রহ নাই। ফলে পাবলিক হেলথ আর ফুড সায়েন্স নামক দুটো প্রধান শাখাকে আমাদের বাদ দিতে হচ্ছে। আমরা ছুটছি শুধু মৌলিক পুষ্টিবিজ্ঞানের দিকে।
কথায় বলে না, পরাজয়ে ডরে না বীর? আমি নিজেকে বীর প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম GRE-IELTS নতুন করে দেবো। কিন্তু নতুন করে দিলেই তো খালি হবে না, ভালো স্কোর উঠানোর মত প্রস্তুতিও নেওয়া আবশ্যক, যেটার জন্য আমার হাতে সময় ছিলো না। তাই ঠিক করলাম, এই স্কোর নিয়েই দৌড়াবো। ২০১৬ সালে যেহেতু IELTS-এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, তাই আমাকে অবশ্যই ফল ২০১৬-এ সুযোগ পেতে হবে। ছোটবোন সারা আমেরিকার সব ভার্সিটি ভেজে খেয়েছে, যেখানে পুষ্টিবিজ্ঞান অনুষদ আছে। তাই ওর গাইডলাইনের ঠ্যালায় পড়ে আমি দেড়শো’র মত প্রফেসরকে নক করে ফেললাম। এমনও অবস্থা গেছে, যখন কেউ রিপ্লাই না দিলে আমি সাতবার পর্যন্ত উনাকে মেইল পাঠিয়েছি। মোট কথা, আমি মরিয়া হয়ে গেছি। হয় এস্পার (আমেরিকা), নয় এস্পার (আমেরিকা)। অভিধান থেকে ওস্পার (হাল ছেড়ে দেওয়া) শব্দটা শিফট+ডিলিট মারলাম। এবার বুঝলাম দুইশো তিনশো প্রফেসরকে মেইল পাঠানোর উপকারিতা। আপনি যত বেশি প্রফেসরকে নক করবেন, পজিটিভ রিপ্লাই পাওয়ার সম্ভাবনা তত বাড়বে। দিন শেষে কোথায় এপ্লাই করবেন, সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আপনার হাতে। তাই যত বেশি পজিটিভ রিপ্লাই পাবেন, এপ্লাই করার সুযোগ তত বাড়বে, অ্যাডমিটেড হওয়ার সুযোগও বাড়বে।
ফল ১৫-এর জন্য মেইল করতে শুরু করেছিলাম সেপ্টেম্বর মাস থেকে (GRE স্কোর জানার পর)। সর্বোচ্চ চল্লিশজনের মত প্রফেসরকে নক করে জেনেরিক উত্তর পেয়েছিলাম সাত আটজনের কাছ থেকে। কিন্তু এবার শুরু করলাম মে মাস থেকে। আগেরবার শুধু একটা নির্দিষ্ট টপিকের উপর যারা কাজ করেন, তাদের খুঁজে বের করেছিলাম। এবার শুধু একটা নয়, বরং নিজের পছন্দকে বিস্তৃত করে চার পাঁচটা টপিক নির্বাচন করলাম। ফলে অনেক বেশি প্রফেসরকে নক করতে পারলাম। মেইলিং ফরম্যাট আর সিভি ফরম্যাট বদলে ফেললাম আগাগোড়া। মোটের উপর, গতবারের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে নিজেকে তুলে ধরলাম। তারপর ধুমসে মেইল দিতে শুরু করলাম। ধুমসে রিপ্লাইও পেতে থাকলাম। মজাই মজা! এবার আর কাজটাকে বিরক্তিকর লাগলো না। বরং দারুণ উত্তেজনাকর মনে হলো। প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচজন, বেশিপক্ষে দশ-পনেরোজন প্রফেসরকে মেইল দেওয়া শুরু করলাম। যিনি উত্তর দেন না, উনাকে আবার সাতদিন পর নক করতাম। এভাবে চক্র চলতে থাকতো। হোক না নেতিবাচক রিপ্লাই, তবু তো পেতাম! অনেক প্রফেসর নম্রভাবে “না” করার পাশাপাশি আমার প্রোফাইলের প্রশংসাও করতেন। ফলে তলানিতে এসে ঠেকা আত্মবিশ্বাস জেগে উঠতো। একসময় আবিষ্কার করলাম, আমি যে ল্যাব বেইজড টপিকগুলো নিয়ে কাজ করতে চাই, সেগুলোতে খুব একটা ফান্ড নেই। তার উপর সেগুলোতে কাজ করতে গেলে যে পরিমাণ ল্যাবরেটরি অভিজ্ঞতা দেখতে চান প্রফেসররা, সেটা আমার একেবারেই নেই। বুঝলাম, সময় এসেছে ল্যাব বেইজড টপিক থেকে সরে আসার। আরও বেশি ফ্লেক্সিবল হয়ে এবার আমাকে তাকাতে হবে কমিউনিটি নিউট্রিশনের বিভিন্ন টপিকের দিকে। এই বিষয়টাকে আমি এড়িয়ে চলতে চেয়েছিলাম কারণ কমিউনিটিতে গিয়ে কাজ করার হ্যাপা আমার ভালো লাগে না। অনার্সের সময় গবেষণা করতে গিয়ে যথেষ্ট ভুগেছিলাম। কিন্তু ভার্সিটি ঘেঁটে দেখলাম, আমেরিকায় এই বিষয়টার উপরেই বেশি ফান্ড দেওয়া হচ্ছে। গবেষণাগারে যে গবেষণা হয়, সেটার প্রয়োগ তো কমিউনিটিতেই হবে, নাকি? তাই হয়তো এই ব্যাপারটার উপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। আমিও তাই কমিউনিটির প্রফেসরদের পিছেই ছোটা শুরু করলাম।
তারপরও খুব একটা সুবিধা হলো না। যেমন, একজন প্রফেসর আমার প্রোফাইলের অনেক প্রশংসা করে স্কাইপ ইন্টার্ভিউ নিতে চাইলেন। আমি তো খুশিতে বাঁচি না। এতদিন পর হয়তো আমার অপেক্ষার অবসান ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু ওমা! কিছুদিন পর প্রফেসর জানালেন, বিভাগীয় ঝামেলার কারণে তিনি এই বছর কোনো স্টুডেন্ট নিতে পারবেন না। তৃতীয়বারের মত অনুভব করলাম স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। তারপরও হতাশ হলাম না। হাতে এখনও প্রফেসরদের বিশাল তালিকা ধরা। একদম শেষজন পর্যন্ত দেখবো। গত বছরের সকল ভুল ঝেটিয়ে দূর করে এখন আমি অনেক অভিজ্ঞ আর শক্ত একজন পিছু ধাওয়াকারী। দিনে দিনে sent মেইলের সংখ্যা চারশো ছাড়িয়ে গেলো। তুলনায় ইনবক্সে মেইলের সংখ্যা নগণ্য। হাল ছাড়লাম না। আমি সব ভার্সিটির নাম এবং প্রফেসরের বিস্তারিত তথ্য দিয়ে যে তালিকাটা বানিয়েছিলাম, সে অনুযায়ী প্রথমে সব ল্যাব বেইজড গবেষকদের নক করেছিলাম। পজিটিভ উত্তর না পাওয়ায় কমিউনিটি নিউট্রিশনের প্রফেসরদের নক করেছিলাম। সে সূত্রে টেনেসি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি নিউট্রিশনের প্রফেসরদের নক করতে করতে চলে এসেছিলো জুলাই মাস। তখন অন্য কোথাও থেকে মনমত রিপ্লাই না পেয়ে আমার মন খারাপ। বিধ্বস্ত অবস্থায় নক করলাম একজন প্রফেসরকে। প্রথম দেখাতে ইনাকেই আমার সবচেয়ে বেশি মনে ধরলো কারণ উনার কাছে ফান্ড আছে। প্রফেসর কোনো উত্তর দিলেন না। তিনবার মেইল করেও যখন উত্তর পেলাম না, তখন অন্য প্রফেসরদের ধরলাম। কেউই উত্তর দিলেন না। শুধু একজন বললেন, “আপাতত স্টুডেন্ট নিচ্ছি না, তবে যোগাযোগ রাখো। ভবিষ্যতে নিতে পারি।” মাঝ সমুদ্রে এটাই আমার জন্য খড়কুটো হয়ে রইলো। বাকি ছিলেন একজন। তাকে নক করবো কিনা ভেবে ক’দিন কাটালাম। জেনেরিক রিপ্লাই পেতে পেতে এতো হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম যে, আরেকজনের কাছ থেকে জেনেরিক রিপ্লাই হজম করার মত মানসিক শক্তি ছিলো না। তারপরও অভ্যাসবশত মেইল পাঠালাম। পরদিন হঠাৎ নোটিফিকেশন এলো নতুন মেইলের। তড়িঘড়ি মেইল খুলে দেখি শেষ প্রফেসর উত্তর দিয়েছেন। ঝাঁপিয়ে পড়ার বদলে ঢকঢক করতে থাকা বুক নিয়ে ক্লিক করলাম ইনবক্সে। বেশি কিছু লেখেননি তিনি, শুধুমাত্র একটা বাক্য “Would you like to set up a call (skype) to chat?” অনেকক্ষণ ধরে বাক্যটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। উপরে নিচে আর কিছু লেখা নেই। পুরো মেইলে শুধু একটাই বাক্য, অথচ কী শক্তিশালী!
এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আমি কোনো প্রফেসরের কাছ থেকে স্কাইপ ইন্টার্ভিউয়ের প্রস্তাব পেলাম। শুনেছি এই ইন্টার্ভিউ নাকি তাদেরকেই দিতে বলা হয়, যাদের প্রোফাইল প্রফেসরের পছন্দ হয়। তার মানে আমার সিভি উনার পছন্দ হয়েছে। হঠাৎ মনে হলো, আনন্দে দম বন্ধ হয়ে আসছে। প্রায় দেড়শ প্রফেসরকে তিনবার করে নক করার পর স্কাইপ ইন্টার্ভিউ পর্যন্ত আসতে পারাটা আমার কাছে অনেক বেশি কিছু। নির্দিষ্ট দিনে প্রফেসরের সাথে স্কাইপ ইন্টার্ভিউয়ে বসলাম, ইন্টার্ভিউ নিয়ে উনি খুব খুশি হলেন। এছাড়া আমার উপায়ও ছিলো না। এই একটা সুযোগই আমি পেয়েছি। উনাকে মুগ্ধ করতে না পারলে ২০১৬ সালের ফল সেশনও হাতছাড়া হয়ে যাবে। অবশ্য উনার সাথে ইন্টার্ভিউ শেষ করার পর নিরাপদ থাকার জন্য আমি আরও কয়েকজন প্রফেসরকে নক করেছিলাম। ন্যাড়া বেলতলায় একবারই যায় কিনা! একসময় একজন উত্তর দিলেন, “তোমার প্রোফাইল পছন্দ হয়েছে। কিন্তু আমার হাতে এই মুহূর্তে ফান্ড নেই। তুমি এপ্লাই করে রাখো, ফান্ড পেলে তোমাকে নেবো।” আমি এটাকে দ্বিতীয় অপশন হিসেবে রাখলাম। এরপর শুরু হলো রিকোমেন্ডেশন লেটার যোগাড় করার যুদ্ধ। পুরো অ্যাডমিশন প্রক্রিয়ায় এই বিষয়টা আমাকে যেভাবে ভুগিয়েছে, তার মত ভোগান্তি আর কিছুতেই ছিলো না। পাঠকদের বিরক্তি লেগে যাবে যদি আমি সবগুলো ঝামেলার বর্ণনা দিই। তবু একজন প্রফেসরের কাহিনি না বলে পারছি না। উনি আমাকে অনলাইনে লেটার দেবেন বলে আশ্বস্ত করেছিলেন। দিন যায়, মাস যায়, সেই লেটার আর পাই না। দু’তিনদিন ফোন করে অনুরোধ করলাম দ্রুত লেটারটা সাবমিট করার জন্য। এতে হলো হিতে বিপরীত। উনি লেটার পূরণ করা শুরু করে উধাও হয়ে গেলেন। কোনো টিচার একবার ওয়েবসাইটে লগইন করে ফেললে রিকোমেন্ডারের নাম পাল্টানো যায় না। যখন দেখলাম ডেডলাইন চলে আসছে এবং উনার লেটার পূরণ করা ঝুলে আছে, উনাকে ফোন দেওয়া শুরু করলাম। উনি আমার নাম্বার “রিজেক্ট লিস্ট”-এ ঢুকিয়ে দিলেন। কোনোমতেই ফোন যায় না দেখে অন্য নাম্বার থেকে চেষ্টা করলাম, দেখলাম ঠিকই যাচ্ছে। কিন্তু উনি কোনো অচেনা নাম্বার ধরেন না। ফলে আমি বলতেও পারছি না, কতো জরুরি ভিত্তিতে লেটারটা আমার লাগবে।
প্রচণ্ড আত্মসম্মানে লাগলো। যাহ্, লাগবেই না আপনার রেকোমেন্ডেশন। ভার্সিটিকে বললাম, “অমুক প্রফেসর অসুস্থ বলে অনলাইন লেটার পূরণ করতে শুরু করলেও পুরো কাজ শেষ করতে পারেননি। আমি কি অন্য কারও পেপার লেটার পাঠাতে পারবো?” উত্তরে “হ্যাঁ” শুনে ধরলাম আরেকজন টিচারকে। উনি ডেডলাইনের দশদিন আগে আমাকে পেপার লেটার দিলেন। সেটা পাঁচদিনের ভেতরে ভার্সিটিতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলাম। কী যে একটা পরিস্থিতি গেছে আমার! এক সপ্তাহে মোট পাঁচবার উনার বাসায় যেতে হয়েছে, অফিস শেষ করে। কী যে ক্লান্ত লাগতো, কী যে কান্না পেতো, কী যে হতাশ হতাম! তবে একটা জিনিস মনে রাখবেন। যেকোনো সমস্যায় গ্র্যাড কোঅর্ডিনেটরকে মেইল পাঠাবেন। অনেক সময় দেখা যায়, গ্র্যাজুয়েট কোঅর্ডিনেটর একজন প্রফেসর। তখন সমস্যা হয়। কারণ একজন প্রফেসরকে বারবার মেইল দিয়ে বিরক্ত করা সাজে না। তখন খুঁজে বের করবেন ডিপার্টমেন্টের আর কাকে মেইল দেওয়া যায়। অনেক সময় ডিপার্টমেন্টে স্পেশালিস্ট কেউ থাকেন শুধুমাত্র আবেদন প্রক্রিয়া সামাল দেওয়ার জন্য। তাকে মেইল পাঠাতে পারেন। হয়ত আপনার বিভিন্ন সমস্যা শুনতে শুনতে তারা বিরক্ত হবেন, কিন্তু গরজটা আপনার। আমি নিজে টেনেসি বিশ্ববিদ্যালয়ের এডমিনিস্ট্রেটিভ স্পেশালিস্টকে অনেক জ্বালিয়েছি। এক রিকোমেন্ডেশন লেটারের সমস্যা নিয়েই উনাকে পাঁচবার মেইল দিয়েছি। কিন্তু উনি কখনও বিরক্ত হননি বা হলেও আমাকে বুঝতে দেননি। আমি সত্যি মুগ্ধ উনার আচরণে।
এরপর শুরু হলো ভর্তি ফলাফল আসার অপেক্ষা। এটা যে কী বিচ্ছিরি একটা সময়, সব আবেদনকারীই টের পান। দুরু দুরু বুকে প্রতিটা দিন কাটে। কখন যে আসবে কাঙ্ক্ষিত উত্তর! যদিও গ্র্যাজুয়েট কোঅর্ডিনেটরকে মেইল করে নিশ্চিত হয়েছি ফেব্রুয়ারিতে আসবে সিদ্ধান্ত, তবু খালি মনে হয়, আগেও তো চলে আসতে পারে! কে জানে, এবারও হতাশ হতে হবে নাকি ঠোঁটের কাটা বড় হয়ে যাবে হাসতে হাসতে? কি পাঠক, ভাবছেন শেষ হাসি আমিই হেসেছি? উঁহু! UTK থেকেও এলো রিজেকশন লেটার। এবার আর কান্না টান্না পায়নি, বরং মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেলো একটা ধারণা – আমার হবে না। পরপর তিন বছর ব্যর্থ। হয় এই প্রোফাইল দিয়ে হবে না, নয় আমার কাজ করার পদ্ধতি ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু কোথায় হচ্ছে গাফিলতি?
দ্বিতীয় পর্ব এখানে