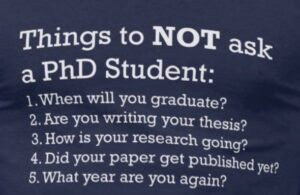প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব, তৃতীয় পর্ব, চতুর্থ পর্ব
১) পছন্দের প্রফেসরদের সাথে ভলান্টিয়ার কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করুন। অনেক প্রফেসর হয়ত সিস্টেম্যাটিক রিভিউ নিয়ে কাজ করছেন যেখানে ডাটা এক্সট্র্যাকশন বা স্ক্রিনিং করতে হবে। আপনি সেসব কাজে অংশ নিতে পারেন কিনা জিজ্ঞেস করে দেখুন। এজন্য এসব বিষয়ে জ্ঞান থাকা জরুরী। যখন ব্যাচেলর বা মাস্টার্স করছেন, তখন দেশের সুপারভাইজারের কাছ থেকে পেপার কীভাবে রিভিউ করতে হয় বা সিস্টেম্যাটিক রিভিউ কীভাবে করে, সেগুলো শিখে নিন। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি শিক্ষার্থীদের সাথে কোলাবরেশনে প্রজেক্ট করুন। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স/মাস্টার্স পর্যায়ে পেপার পাব্লিশ করতে দেখছি পুষ্টি এবং খাদ্যবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের। আমার সময়ে (২০০৭-২০১৩) এত সচেতনতা দেখিনি। তো, এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে গবেষণার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জন করুন।
প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন প্রফেসরের সাথে কাজ করতে চাইবেন? এতে সুবিধা কী? সুবিধা হল, আপনার সামর্থ্যের ব্যাপারে প্রফেসরের মনে একটা ধারণা তৈরি হবে। ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থী এবং গবেষক হিসেবে আপনি কেমন হবেন, সেটা সম্পর্কে কিছুটা হলেও আন্দাজ করা যাবে। একদম নতুন কাউকে নেওয়ার পরিবর্তে তিনি হয়ত আপনাকে নিতেই আগ্রহী হবেন। আপনাকে কোন বিষয়ে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ দেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে হয়ত ধারণা পরিষ্কার হবে। অনেক প্রফেসর আবার স্কাইপ ইন্টার্ভিউ নেওয়ার আগে/পরে একটা এসাইনমেন্ট দেন (আমি যার সাথে কাজ করতে যাচ্ছি, তিনিও আমাকে এসাইনমেন্ট দিয়েছিলেন)। সেটা সাবমিট করলে ফিডব্যাকও দেন। এই কাজ করা হয় শিক্ষার্থী সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য। এই কাজই আপনি নিজে থেকে করার আগ্রহ দেখাতে পারেন ভলান্টিয়ারিংয়ের মাধ্যমে।
২) লিংকডইন এবং টুইটারে পছন্দের প্রফেসর, ল্যাব এবং প্রোগ্রামের পেইজ অনুসরণ করুন। এসব জায়গায় ফান্ড বিষয়ক প্রচুর পোস্ট দেওয়া হয়। প্রফেসররা নিজেরা স্টুডেন্ট খুঁজলে তো পোস্ট দেনই; অন্য আরেকজন প্রফেসরের ওপেনিং নিয়েও অনেকে পোস্ট দিয়ে থাকেন। আমি এরকম প্রচুর পোস্ট দেখেছি যেখানে একজন প্রফেসর আরেকজনের ল্যাব ওপেনিং সম্পর্কে জানাচ্ছেন। একই কথা খাটে আপনার পছন্দের মেজরে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন এমন লোকজনের সাথে লিংকডিনে কানেক্টেড হওয়ার ব্যাপারে। দেশের ভেতর এবং বাইরে যারা পুষ্টি বা গণস্বাস্থ্যের বিভিন্ন কন্সেন্ট্রেশনে গবেষণা করছেন, তাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন। একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা কত সাংঘাতিক! আমি নোবিপ্রবির এক আপুর সাথে লিংকডিনে কানেক্টেড আছি যিনি পুষ্টিতে পড়ালেখা করেছেন। উনার সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই, কিন্তু উনার গবেষণা আমার ভাল লাগে বলে কানেক্টেড হয়েছিলাম। তিনি ২০২০ সালের অক্টোবরে একটা পোস্টে লাইক দিয়েছিলেন যেটা আমার হোমফিডে এসেছিল। পোস্টটা ছিল টেক্সাস এঅ্যান্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি বিভাগে “ফল ২০২১-এর জন্য অ্যাসিস্টেন্টশিপ দেওয়া হচ্ছে” বিজ্ঞাপন। সেই বিজ্ঞাপন দেখে আমি দ্রুত ওদের ওয়েবসাইটে যাই। এপ্লাই করার ডেডলাইন কবে, অ্যাডমিশন কি সেন্ট্রাল নাকি প্রফেসর ম্যানেজ করা লাগে, সবকিছু যাচাই করি। প্রফেসরদের তালিকা থেকে পছন্দের প্রফেসর বাছাই করে যোগাযোগ শুরু করি। প্রোগ্রামটা সেন্ট্রালি অ্যাডমিশন দেয় এবং ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীরা রোটেশনের মধ্য দিয়ে যায়। কিন্তু কারো যদি পছন্দের প্রফেসর থাকে এবং ঐ প্রফেসর তাকে নিতে চান, তাহলে রোটেশন এড়িয়ে সরাসরি ঐ প্রফেসরের সাথে কাজ শুরু করা যায়। আমার হাল শেষ পর্যন্ত তাই হল। এক প্রফেসরকে এমন পছন্দ হল যে, উনার পিছু ছাড়লাম না। ছয় মাস উনার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রইল। অবশেষে মার্চে উনি নিশ্চিত করলেন আমাকে নেওয়ার ব্যাপারে। দেখেছেন, কীভাবে একজন আপুর একটা লাইক আমাকে পছন্দের প্রফেসরের সাথে পিএইচডি করার সুযোগ এনে দিল?
৩) আপনার পছন্দের প্রোগ্রামে যদি বর্তমান বা প্রাক্তন কোনো বাংলাদেশী শিক্ষার্থী থেকে থাকেন, তাদেরকে ইমেইল দিতে পারেন। তারা হয়ত ডিপার্টমেন্টের ইন্টারনাল অপরচুনিটি সম্পর্কে জানবেন। না জানলেও ক্ষতি নেই। বিভিন্ন প্রফেসর এবং তাদের ল্যাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য উনাদের সাথে কথা বলতে পারেন। সবচেয়ে ভাল হয়, যে প্রফেসরের সাথে আপনি কাজ করতে চান, উনার অধীনে যেসব শিক্ষার্থী আছেন, তাদের সাথে যোগাযোগ করলে। আমি কোনো প্রোগ্রাম ঘাঁটলে সেখানে বাংলাদেশের কেউ আছে কিনা জানার চেষ্টা করি। কারেন্ট স্টুডেন্ট, পিপল, বা এলামনাই অপশনে এসব তথ্য থাকার কথা। নতুবা গুগল তো আছেই। Bangladeshi nutrition students at X university লিখলে কিছু না কিছু পাওয়ার কথা। সাথে লিংকডইনেও চেক করবেন। উনাদের কাছ থেকে বর্তমান ট্রেন্ড কী, কোনটা হট টপিক, কোন টপিকে ফান্ড বেশি, কোন টপিক নিয়ে গবেষণা করলে পিএইচডি শেষে চাকরির রমরমা বাজার দেখবেন ইত্যাদি বিষয়েও জানতে চাওয়া যায়।
একটা কথা মাথায় রাখতে হবে। কাউকে ইমেইল দিলেই যে তিনি আপনাকে রিপ্লাই দিবেন, এমনটা নাও হতে পারে। আমি অনেক বাংলাদেশীকে ইমেইল দিয়ে রিপ্লাই পাইনি। হয়ত উনারা ব্যস্ত ছিলেন, সময় পাননি/ভুলে গেছেন, হয়ত আমার ইমেইল স্প্যামে চলে গিয়েছিল। অনেক কিছুই হতে পারে। এতে মন খারাপের কিছু নেই, অন্যদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণেরও কিছু নেই।
৪) দেশী শিক্ষার্থী খুঁজে বের করার আরেকটা কারণ আছে। আপনি যে প্রফেসরের সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক, উনার ল্যাবে যদি বর্তমানে বাংলাদেশী শিক্ষার্থী থাকেন, বা আগে কোনো বাংলাদেশী পাশ করে থাকেন, তাদের ভাল পার্ফর্মেন্সের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে আরও বাংলাদেশী শিক্ষার্থী নেওয়া হতে পারে। আগের দেশী শিক্ষার্থীরা যদি সুনাম তৈরি করেন, পরবর্তী দেশী শিক্ষার্থীদের উপর ডিপার্টমেন্টের ভরসা বাড়ে। যেসব ডিপার্টমেন্টে তাই দেশী শিক্ষার্থী পাবেন, সেখানকার প্রফেসরদের একবার হলেও নক করে দেখুন। আমি ওহাইও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসরকে নক দিয়েছিলাম। বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে উনি দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, “I have one wonderful student from your country, Dr “Y”, and I am definetly interested in you.” তার মানে বাংলাদেশী ঐ আপু দারুণ পারফর্মেন্স দেখিয়েছেন এবং উনার কারণে প্রফেসর আমার উপর কিছুটা ভরসা পাচ্ছেন। পরে অবশ্য এপ্লাই করিনি। আবার টেক্সাস টেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি বিভাগে বেশ কিছু বাংলাদেশী মাস্টার্স এবং পিএইচডি করছেন। সেখানে আবেদন করার দশদিনের মাথায় আমি টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপসহ অ্যাডমিশন অফার পেয়েছিলাম। এর পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে আমার সার্বিক প্রোফাইল এবং প্রফেসরের সাথে যোগাযোগ। কিন্তু যেসব দেশী শিক্ষার্থী ওখানে আছেন বা পাশ করে বেরিয়ে গেছেন, তাদের সুনামও কি সাহায্য করেনি আমার উপর অ্যাডমিশন কমিটির ভরসা জাগানোর পিছে? অবশ্যই করেছে!
(চলবে)