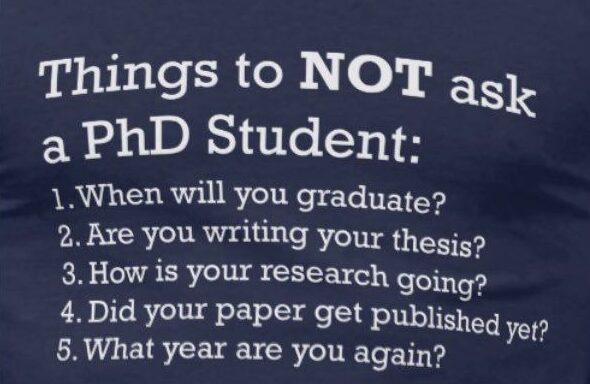Read Time9 Minute, 53 Second
পিএইচডি প্রোগ্রামে ঢুকার জন্য বহুত লাফিয়েছি। অনেক খায়েশ ছিল গবেষণা জগতটাকে নখদর্পণে আনব। সে ইচ্ছা ফল-২০২১ থেকে পূরণ হতে যাচ্ছে। ফল সেশন মানে আগস্ট মাস। কিন্তু এখনই পিএইচডির ওয়ার্কলোডের হালকা ট্রেইলার দেখে ফেললাম। ক’দিন আগে হবু পিএইচডি সুপারভাইজর বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, “একটা প্রজেক্টে যুক্ত হবা নাকি? মেলা কিছু শিখতে পারবা।” প্রজেক্টটা ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। ডেটাবেস সার্চ শেষ। এখন ডেটা স্ক্রিনিংয়ের জন্য আমি যোগ দিতে পারব। চিন্তা করলাম, শেষ কো-অথরের নামটাও যদি আমার হয়, খারাপ কি? বললাম, “অবশ্যই!” এর ক’দিন বাদে সুপারভাইজর আবার গুঁতালেন। “কি রুথ, টেক্সাসে আসার জন্য গোছগাছ করছ নাকি? একটু সময় হবে আরেকটা প্রজেক্টে যোগ দেওয়ার?” আমি আমতা আমতা করলাম। এ কী অবস্থা! ভেবেছিলাম মে, জুন, জুলাই – তিন মাস ধুমসে ঘোরাঘুরি করব। আগামী তিন থেকে চার বছর যেহেতু রোলার কোস্টার রাইড চলবে, তাই তিন মাসে ঘুরে রিচার্জড হয়ে নেব। এখন দেখি সেই তিন বছরের শুরু আগস্ট থেকে নয়, মে থেকেই হয়ে যাচ্ছে।
সুপারভাইজর লেজ জুড়ে দিলেন, “কোনো চাপ নিও না। সপ্তাহে দুই/তিন ঘণ্টা যদি ম্যানেজ করতে পার, আমাকে জানিও।” প্রথম প্রজেক্টেও দুই/তিন ঘণ্টা দিতে হচ্ছে। এটাতেও মাত্র দুই/তিন ঘণ্টা লাগলে সমস্যা হওয়ার কথা না। তাছাড়া পিএইচডি শুরুর আগে যদি গবেষণায় খানিকটা হাত পাকাতে পারি, আমারই লাভ। বললাম, “অবিশ্যি!” সুপারভাইজর খুশি হয়ে বাহবা টাহবা দিলেন। তারপর একদিন কাজ বুঝিয়ে দিলেন। যে মেয়ে এই প্রজেক্ট শুরু করেছে, সে টামুর (TAMU) একজন সিনিয়র। সিনিয়র মানে ব্যাচেলর প্রোগ্রামের শেষ বর্ষে। এখানে প্রথম বর্ষকে বলে ফ্রেশম্যান, দ্বিতীয় বর্ষকে সফোমর, তৃতীয় বর্ষকে জুনিয়র। মেয়েটা প্রি-মেড (Pre-med) ট্র্যাকের। প্রি-মেড মানে ভবিষ্যতে মেডিকেল স্কুলে ঢুকবে। প্রস্তুতি হিসেবে নির্দিষ্ট কোর্সওয়ার্ক শেষ করছে। গবেষণার প্রতি তার বেশ আগ্রহ। বয়স কতই বা হবে? বাইশ, তেইশ। অথচ কি পটপট করে বলে যাচ্ছে আম্ব্রেলা রিভিউ কীভাবে করতে হয়। আমি এখনও ঠিকঠাক জানি না রিভিউয়ের ধরন। মাস্টার্সে একটা সিস্টেম্যাটিক রিভিউ করেছিলাম। সেটা থেকে পাওয়া জ্ঞান এক কণা বালুর সমান। তাই মুসা আমানের মত ভাবি, খাইছে আমারে! কতকিছু জানা বাকি। নিজেকে টাইটানিক ধরলে সামনে আসছে জ্ঞানের বিশাল আইসবার্গ। ধাক্কা সামলাতে পারব তো?
.
ছোট বোন মিষ্টি সবসময় বলে, পিএইচডি একটা লাইফস্টাইল। এর অর্থ হল, পিএইচডিকে জীবন বানিয়ে ফেলতে হবে। যদি ভাবি পিএইচডি আলাদা আর আমার জীবন আলাদা, তাহলে পিএইচডিকে বোঝা মনে হবে। এসব জ্ঞান সে পেয়েছে সাস্কাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পিএইচডি ক্যান্ডিডেটের কাছ থেকে। চরম মেধাবী সেই ছেলের ঝুলিতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি আছে। সাত ঘাটে পানি খাওয়া ছেলেটার অভিজ্ঞতা অবশ্যই ফেলনা কিছু নয়। সে নাকি বলে, সপ্তাহে সাতদিন কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। মনকে এভাবেই প্রস্তুত করে মাঠে নামতে হবে। কাজ করাতে বিরক্তি আসা যাবে না। যা করব, সেটাকে উপভোগ করতে হবে। তাহলে মনে হবে না ‘বাইরের কাজ’ করছি। মনে হবে, যা ভালবাসি, তার পেছনেই সময় দিচ্ছি। কথাটা সত্যি। যখন আমি লেখালেখি করি, তখন আগ্রহ নিয়ে করি। ভালো লাগা থেকে করি। মনে হয় না, ঘাড়ের উপর দায়িত্ব চেপে আছে বলে লিখছি। তাহলে একই কথা গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না কেন? যে বিষয়ে আমার আগ্রহ, সেই বিষয়েই তো পিএইচডি করতে যাচ্ছি। তাহলে সেটা নিয়ে সাতদিন কাজ করতে ভাল লাগবে না কেন?
.
আগে ভাবতাম, যেকোনো প্রফেসরের অধীনে যেকোনো টপিকে ঢুকে গেলেই হল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে মাস্টার্স করতে এসে বাছবিচার করতে শিখেছি। কোর্সওয়ার্ক করতে করতে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জেনেছি। পুষ্টিবিজ্ঞানের জগতে বর্তমান ট্রেন্ড কী, কী নিয়ে গবেষণা করলে চাকরি জীবন ফকফকা, কোন বিষয়ে ফান্ড বেশি, ইত্যাদি ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে শিখেছি। এভাবে নিজের একটা ভালোলাগা তৈরি হয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু টপিকের উপর মন আটকে গেছে। অথচ দেশে থাকতে গণহারে সব ফিল্ডের প্রফেসরকে ইমেইল দিতাম, “আপনার গবেষণা ভাল লাগে। আপনার সাথে কাজ করতে আগ্রহী।” এগুলো যে কত ছেলেমানুষি ছিল, ভাবলে অবাস্তব লাগে। আবার যেকোনো প্রফেসরের আন্ডারে ঢুকে গেলেই যে হল না, সেটাও করুণ এক ঘটনার মাধ্যমে টের পেয়েছি।
.
যুক্তরাষ্ট্রে মাস্টার্স শুরু করা থেকেই আমার আগ্রহ ছিল ক্যান্সার গবেষণায়। মাস্টার্সের সুপারভাইজর একদিন বললেন, “ক্লিনিকেল রিসার্চ তুমি পেরে উঠবে না। সিস্টেম্যাটিক রিভিউ অ্যান্ড মেটা এনালাইসিস কর।” যদিও আমার ইচ্ছা ছিল ক্লিনিকেল রিসার্চে, কিন্তু উনার কথায় আত্মবিশ্বাস টুটে গেল। নতুন দেশ, নতুন রীতিনীতি। সুপারভাইজর যদি উৎসাহ দেওয়ার বদলে বলেন আমি পারব না, তাহলে নিশ্চয়ই আমি পারব না। ক’দিন পর উনি বললেন, “মেটা এনালাইসিসে আমার অভিজ্ঞতা নেই। তুমি শুধু সিস্টেম্যাটিক রিভিউ কর।” মেটা এনালাইসিসে আমারও অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই আর কথা না বাড়িয়ে সিস্টেম্যাটিক রিভিউয়ে মন দিলাম। কিন্তু উনার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা তৈরি হয়ে গেল। মনে হল, অনুপ্রাণিত করার বদলে উনি আমাকে খালি দাবাতে চাইছেন। উনার সাথে কাজ করতে করতেই মাথায় বাছবিচারের ব্যাপারটা ফিলিপ্স বাত্তির মত জ্বলে উঠল। বুঝলাম, কোনো প্রফেসরের আন্ডারে ঢুকার আগে উনাকে ভালমত যাচাই করা দরকার। উনি মানুষ হিসেবে কেমন, উৎসাহ দেন নাকি চাপ প্রয়োগ করেন, নিজের মতামত চাপিয়ে দিতে চান নাকি শিক্ষার্থীর মতামতের মূল্য দেন, ইত্যাদি বুঝা দরকার। অনলাইন ইন্টার্ভিউয়ের মাধ্যমে কথা বলে বলে ধারণা নেওয়া দরকার।
.
সেটাই করলাম পিএইচডিতে আবেদনের বেলায়। যেসব প্রোগ্রামে অ্যাডমিশন পেলাম, সবগুলোর প্রফেসরের সাথে মিটিং করলাম। প্রশ্ন করতে করতে ঝাঁঝরা করে ফেললাম উনাদের। বুঝার চেষ্টা করলাম কে কতটা সাপোর্টিভ। কার কতটা ভাল ধারণা আছে আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। হাজার হোক, আমি উনাদের ল্যাব থেকে ডিগ্রি নিয়ে বের হব। বের হওয়ার পর আমার ভবিষ্যৎ কী, সে সম্পর্কে যদি উনাদের ধারণা না থাকে, কীভাবে কী? সবচেয়ে ভাল লাগল টামুর প্রফেসরকে। তাই উনি পজিশন অফার করার সাথে সাথে একসেপ্ট করে ফেললাম। তখনও জানতাম না উনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্টডক করেছেন। যখন জানলাম তখন হাঁ মুখ বন্ধ হচ্ছিল না। মা রে মা! কী বিল্লু। যা হোক, এরপরই উনি আমাকে দুটো প্রজেক্টের সাথে জুড়ে দিলেন। সাথে ধারণা দিলেন পিএইচডির সময় কোন কোন টপিকের উপর গবেষণা করার সুযোগ আছে। বুঝতে পারলাম, সিক্স ফ্ল্যাগ থিম পার্কের মত একখানা রোলার কোস্টারে চড়তে যাচ্ছি। তবে সময়ই বলে দেবে সেটা কোস্টার থেকে অতি জঘন্য ফ্রি ফলে পরিণত হবে কিনা!